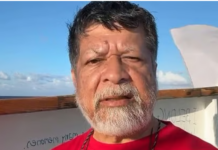যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার বাতিল করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা নির্বাহী আদেশ বেশ কিছু আইনি চ্যালেঞ্জের ও অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।
প্রায় ১৬০ বছর ধরে মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী এমন নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে যে দেশটিতে জন্ম নেওয়া যে কেউই একজন মার্কিন নাগরিক হবেন।
কিন্তু ট্রাম্প অবৈধভাবে বা অস্থায়ী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অভিবাসীদের সন্তানদের নাগরিকত্বের অধিকার অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর নীতির অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। তবে তাঁর এ পদক্ষেপে জনসমর্থন আছে বলেও মনে হচ্ছে। এমারসন কলেজের একটি জরিপে দেখা গেছে, এ ক্ষেত্রে ট্রাম্পের বিরোধিতার পরিবর্তে অনেক বেশি মার্কিন নাগরিক তাঁর পক্ষে আছেন।
বিশ্বজুড়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব
জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বা ‘জাস সোলি’ (মাটির অধিকার) বিশ্বব্যাপী খুব বেশি প্রচলিত রীতি নয়।
যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশের মধ্যে একটি, যারা নিজ দেশে জন্ম নেওয়া যে কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব দেয়। এসব দেশের বেশির ভাগই আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত।
এ নিয়মের বিপরীতে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার কিছু অংশের অনেক দেশই ‘জাস সাঙ্গুইনিস’ বা রক্তের অধিকার নীতি মেনে চলে। এ নীতির মূল বক্তব্য হলো—জন্ম যেখানেই হোক না কেন, শিশুরা তাদের মা–বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করবে।
আবার কোনো কোনো দেশে এ উভয় নীতির সমন্বয়ও দেখা যায়। স্থায়ী বাসিন্দাদের সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়ার নিয়মও দেখা যায় এসব দেশে।
যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক জন স্ক্রেন্টনি বিশ্বাস করেন, আমেরিকা মহাদেশজুড়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বা জাস সোলি প্রচলিত থাকলেও এ ক্ষেত্রে প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্র স্বতন্ত্র কারণে এ রীতি গ্রহণ করেছিল।
আমেরিকা মহাদেশজুড়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বা ‘জাস সোলি’ প্রচলিত থাকলেও এ ক্ষেত্রে প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্র স্বতন্ত্র কারণে এ নীতি গ্রহণ করেছিল।
জন স্ক্রেন্টনির মতে, কিছু দেশ দাস ও সাবেক দাসদের জন্য জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের নীতি গ্রহণ করেছিল। কিছু দেশ একেবারেই ভিন্ন কারণে এ রীতি গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্বের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষদের আইনি স্বীকৃতি দিতে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল।
তবে স্ক্রেন্টনি যুক্তি দেন যে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায় সব দেশের মধ্যে একটি মিল পাওয়া যায়। আর তা হলো, ‘সাবেক উপনিবেশের মর্যাদা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নিজেদের একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা।’
বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক স্ক্রেটনি বলেন, ‘কাকে নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে ও কীভাবে জাতি-রাষ্ট্রকে শাসনযোগ্য করে তুলতে হবে, সেসব সম্পর্কে দেশগুলোকে কৌশলী হতে হয়েছিল। অনেক দেশ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিধান তৈরি করেছিল।’
জন স্ক্রেন্টনি আরও বলেন, কোনো কোনো দেশ ইউরোপ থেকে অভিবাসনকে উৎসাহিত করতে নাগরিকত্বের বিধান রেখেছিল। আবার কোনো কোনো দেশ নিশ্চিত করেছিল যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সাবেক দাস ও তাঁদের সন্তানদের পূর্ণ সদস্য (নাগরিক) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তাঁদের রাষ্ট্রহীন রাখা হবে না। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কৌশল ছিল। সেই সময়টি হয়তো চলে গেছে।

নীতিমালার পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধ
জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার কঠোর বা বাতিল করে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেশ কয়েকটি দেশ তাদের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছে। এর মূল কারণ হলো, অভিবাসন, জাতীয় পরিচয় ও তথাকথিত ‘জন্ম পর্যটন’ নিয়ে উদ্বেগ। ‘জন্ম পর্যটন’ বলতে বোঝায়, যখন কেউ সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য অন্য দেশে ভ্রমণ করেন।
উদাহরণস্বরূপ, ভারত একসময় দেশটির মাটিতে জন্মগ্রহণকারী যেকোনো ব্যক্তিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব দিত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবৈধ অভিবাসনজনিত উদ্বেগের কারণে দেশটি এ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে।
২০০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ভারতে জন্ম নেওয়া একটি শিশু শুধু তখনই দেশটির নাগরিক বলে বিবেচিত হন, যখন তার মা–বাবা উভয়ই ভারতীয় হন। এ ক্ষেত্রে শিশুর মা–বাবার একজন ভারতীয় নাগরিক হলে অন্যজনকে বৈধ অভিবাসী হতে হবে।
আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশ ঐতিহাসিকভাবে ঔপনিবেশিক যুগের আইনি ব্যবস্থার অধীন জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নীতি অনুসরণ করত। স্বাধীনতা লাভের পর দেশগুলো এ নীতি পরিত্যাগ করে। এখন এসব দেশের বেশির ভাগেই শিশুর জন্মসূত্রে নাগরিক হওয়ার জন্য কমপক্ষে একজন অভিভাবককে দেশটির নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হতে হয়।
এশিয়ার বেশির ভাগ দেশে নাগরিকত্ব আরও বেশি নিয়ন্ত্রণমূলক। এসব দেশে মূলত বংশধারাই নাগরিকত্ব নির্ধারণ করে। চীন, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলোয় এ নীতি দেখা যায়।
ইউরোপেও নাগরিকত্বের নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। আয়ারল্যান্ড ছিল এ অঞ্চলের সর্বশেষ দেশ, যারা অবাধে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অনুমতি দিয়েছিল।
২০০৪ সালের জুনে অনুষ্ঠিত এক জরিপের পর আয়ারল্যান্ড এ নীতি বিলুপ্ত করে। জরিপে ৭৯ শতাংশ ভোটার একটি সাংবিধানিক সংশোধনী অনুমোদন করেন, যেখানে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের জন্য কমপক্ষে একজন অভিভাবককে দেশটির নাগরিক, স্থায়ী বাসিন্দা অথবা আইনিভাবে অস্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
আয়ারল্যান্ড সরকার বলেছে, বিদেশি নারীরা তাঁদের সন্তানদের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাসপোর্ট নিশ্চিত করতে সন্তান জন্ম দিতে আয়ারল্যান্ডে পাড়ি জমাতেন। এ কারণেই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নীতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ছিল।
জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি ঘটেছিল ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে। সেখানে ২০১০ সালে একটি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসীদের সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিল করতে নাগরিকত্বের নতুন সংজ্ঞায়ন করা হয়েছিল।
পরে ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে এ–সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। ১৯২৯ সালের পর জন্ম নেওয়া মানুষেরাও এ সিদ্ধান্তের আওতায় পড়েন। এর মধ্য দিয়ে হাজারো মানুষের ডোমিনিকান জাতীয়তা কেড়ে নেওয়া হয়। তাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন হাইতির বংশোদ্ভূত। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো সতর্ক করেছিল যে এ সিদ্ধান্ত অনেককে রাষ্ট্রহীন করে দিতে পারে। কারণ, তাঁদের কাছে হাইতির কাগজপত্রও ছিল না।
আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো ও আন্ত–আমেরিকান মানবাধিকার আদালত এ পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল।
পরে জনরোষের ফলে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র ২০১৪ সালে একটি আইন পাস করে, যেখানে অভিবাসীদের ডোমিনিকান বংশোদ্ভূত শিশুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিশেষ করে হাইতির বংশোদ্ভূতদের পক্ষে যায় আইনটি।
স্ক্রেন্টনি নাগরিকত্বের নীতিতে এমন সব পরিবর্তনকে একটি বৃহত্তর বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা এখন গণ–অভিবাসন ও সহজ পরিবহনের যুগে আছি। এমনকি সমুদ্রপথেও অভিবাসী হয়ে আসার ঘটনা ঘটছে। এখন মানুষও নাগরিকত্ব পেতে কৌশলী ভূমিকা নিচ্ছেন। এসব কারণেই আমরা এখন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে বিতর্ক দেখছি।’
আইনি চ্যালেঞ্জ
জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার বাতিল–সংক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডেমোক্র্যাট–শাসিত অঙ্গরাজ্য ও শহর, নাগরিক অধিকার গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবিশেষে কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করেছেন।
এ ধরনের মামলায় দুজন ফেডারেল বিচারক বাদীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। গত বুধবারও মেরিল্যান্ডের ডিস্ট্রিক্ট বিচারক ডেবোরা বোর্ডম্যান বাদীদের পক্ষে দাঁড়ান।
এই বিচারক পাঁচ অন্তঃসত্ত্বা নারীর পক্ষ নেন, যাঁরা যুক্তি দিয়েছেন যে তাঁদের সন্তানদের নাগরিকত্বের অধিকার অস্বীকার করার মাধ্যমে মার্কিন সংবিধান লঙ্ঘন করা হবে।
বেশির ভাগ আইনবিশেষজ্ঞ একমত হয়েছেন যে ট্রাম্প নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার বাতিল করতে পারবেন না।
ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংবিধানবিশেষজ্ঞ সাইকৃষ্ণ প্রকাশ বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত আদালতই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। এ ব্যাপারে তিনি (ট্রাম্প) নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।’ আদালতে বিচারাধীন থাকায় এ–বিষয়ক নির্বাহী আদেশ এখনো কার্যকর হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে রক্ষণশীল বিচারকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে উঠলে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীকে তাঁরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়।
ট্রাম্পের বিচার বিভাগ যুক্তি দিয়েছে, এটি (১৪তম সংশোধনী) শুধু স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের সন্তানেরা জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক হতে পারবেন না।
কিন্তু অন্যরা এ অবস্থানের বিরোধিতা করে বলেছেন, অন্য মার্কিন আইন নথিপত্রহীন অভিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে ১৪তম সংশোধনীও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।
বিবিসি