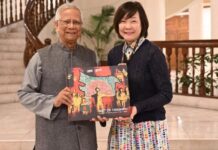রাজধানীর ১৯০ বছরের পুরোনো ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকদের বসার কক্ষে একজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ চলছিল (১১ সেপ্টেম্বর)। তখন ক্লাস শেষ করে এলেন আরেকজন শিক্ষক। ওই শিক্ষক বললেন, তিনি একই সময়ে দুটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিয়েছেন। বাংলা ও কৃষিশিক্ষার। তবে তিনি হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক। শিক্ষকসংকটের কারণেই তাঁকে আরেক বিষয়ের ক্লাস নিতে হচ্ছে।
পাশে বসে ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক। তিনি যোগ করলেন, তাঁকেও নিজের বিষয়ের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষার ক্লাস নিতে হয়। দিনে পাঁচ-ছয়টি করে সপ্তাহে প্রায় ২৫টি ক্লাস নিতে গিয়ে ভালোভাবে পড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলটি সদরঘাট এলাকায় অবস্থিত। এটি অবিভক্ত বাংলার প্রথম সরকারি উচ্চবিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। গত ১১ সেপ্টেম্বর ওই স্কুলে গিয়ে জানা যায়, সেখানে দুই পালায় শিক্ষার্থী প্রায় দুই হাজার। শিক্ষক আছেন মাত্র ৩৯ জন। শিক্ষকের পদসংখ্যা ৫৩। ১৪টি খালি। গড়ে ৫১ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক। শিক্ষকেরা পড়ানোর চাপে হিমশিম খান। ক্লাসে মানসম্মত পড়াশোনা করানো কঠিন হয়ে পড়ে।
বিদ্যালয়টির দুজন শিক্ষার্থী জানাল, তারা নিয়মিত কোচিং ও গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে। একজন বলল, সে বাসায় দুজন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে। খরচ মাসে সাড়ে ছয় হাজার টাকা।
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের এ চিত্র আসলে পুরো দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিচ্ছবি; বরং কোথাও কোথাও পরিস্থিতি আরও খারাপ। শিক্ষকের অভাব, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংকট এবং দুর্বল পাঠদানের কারণে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। এতে পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়ছে অনেকে।
সর্বশেষ বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার ৩৩ শতাংশ।

সচ্ছল মা-বাবা সন্তানদের বাসায় গৃহশিক্ষক রেখে পড়াতে পারেন। কোচিং-বাণিজ্য রমরমা। মধ্যম আয়ের মা-বাবা সন্তানদের কোচিং ও গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াতে গিয়ে বড় ধরনের আর্থিক চাপে পড়ছেন। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা কোচিংয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না, বাসায় গৃহশিক্ষক রাখার সামর্থ্য পরিবারগুলোর নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা পড়াশোনায় ভালো করতে পারছে না।
অবশ্য সরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুলের পেছনে জনগণের করের টাকা ঠিকই খরচ হচ্ছে। বেসরকারি বিদ্যালয়ে উচ্চ হারে বেতন ও ভর্তি ফি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পড়াশোনার মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।
গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া এবং কোচিংয়ের এই প্রবণতা কেবল ঢাকা নয়, সারা দেশে মোটামুটি একই। ময়মনসিংহের একটি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রের বাবা বলেন, তাঁর সন্তান সকালে কোচিংয়ে পড়ে। তারপর বিদ্যালয়ে যায়। এরপর বিকেলে আবারও কোচিং। সন্ধ্যায় বাসায় আসেন গৃহশিক্ষক। তিনি বলেন, খরচ অনেক। কিন্তু কিছু করার নেই। ভালো পড়াশোনা তো করাতে হবে।
অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি বিষয়ে কমিশন গঠন করলেও বাদ দিয়েছে শিক্ষাকে। প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পরামর্শ দিতে শিক্ষাবিদ ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমদকে প্রধান করে কমিটি হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে অগ্রগতি সামান্যই।

শিক্ষার এই সংকট বহু বছর ধরেই চলছে। কোনো সরকারই শিক্ষার মানোন্নয়নে বড় রকমের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে গরিবের সন্তানেরা ভালো মানের পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা এগিয়ে গেছে।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এসে ১১টি বিষয়ে কমিশন গঠন করলেও বাদ দিয়েছে শিক্ষাকে। প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পরামর্শ দিতে শিক্ষাবিদ ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তবে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে অগ্রগতি সামান্যই।
মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক সমস্যা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশির) ভূমিকা নিয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির মহাপরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ আজাদ খান বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে নানামুখী সংকট চলছে। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব আছে। এ কারণে বিদ্যালয়গুলোতে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। কোচিং-প্রাইভেটের মতো বিকৃত পন্থাগুলো বিকল্প হয়ে উঠেছে। ফলে সামর্থ্যহীন পরিবারের শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে।
শিক্ষকদের এমপিও (শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাবদ সরকারি অনুদান), পদ, শাখা খোলা, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) নেতিবাচক ভূমিকা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো পরিপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খাচ্ছিল বলে মনে করেন মাউশির মহাপরিচালক। তিনি আরও বলেন, এখনো সমস্যা রয়ে গেছে। তবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাধানে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষার্থী বেশি, শিক্ষক কম
দেশে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনাকে মাধ্যমিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ধরা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে একই সুপারিশ করা হয়েছিল। কোনোটাই কোনো সরকার বাস্তবায়ন করেনি।
কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে দেশের শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ কর্মী সরবরাহ করা এবং মেধাবীদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাকে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষাবিদেরা বলছেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে যেনতেন শিক্ষা এই দুই উদ্দেশ্যের কোনোটাই পূরণ করতে পারছে না।
মাধ্যমিক পর্যায়ে এখন সাধারণ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করা হয়। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ১৮ হাজার ৯৬৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সাধারণ বা জেনারেল) রয়েছে। এর মধ্যে ৬২৮টি সরকারি। মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ৮১ লাখ ৬৬ হাজার। শিক্ষকসংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৪৭ হাজার। এ ছাড়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ (মাধ্যমিকেও পড়ানো হয়) আছে ১ হাজার ৪৮০টি (৬৩টি সরকারি)। এগুলোতে শিক্ষার্থী প্রায় ১৬ লাখ ১০ হাজার। শিক্ষক প্রায় ৫৫ হাজার।
বেসরকারি স্কুলগুলো আগে নিজেদের মতো করে শিক্ষক নিয়োগ দিত। তবে এখন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের অধীন পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হয়। তবে শিক্ষকের বড় সংকট মূলত সরকারি স্কুলে।
মাউশির তথ্যমতে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য, যা মোট পদের ২০ শতাংশ। শিক্ষকেরা বলছেন, জনবলকাঠামোতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা কম। তার ওপর পদ শূন্য থাকে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপপরিচালকসহ মাধ্যমিকের অন্যান্য পদেও দীর্ঘদিন অনেক পদ শূন্য রয়েছে।
শিক্ষকসংকট দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিসিএসে উত্তীর্ণ, কিন্তু ক্যাডার পদ পাননি (নন-ক্যাডার) এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা চলছে। প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে।
২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে ২০১৮ সালের মধ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১: ৩০-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য ছিল (প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক)। কিন্তু সরকারি বিদ্যালয়ে এখনো গড়ে প্রতি ৩৭ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। যদিও বিদ্যালয় ভেদে তা কোথাও কোথাও আরও বেশি।
সরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল। অথচ এই বিদ্যালয়ে প্রায় এক বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যিনি আছেন, তিনিও চলতি দায়িত্বে রয়েছেন। তিনিই রুটিন দায়িত্ব হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কাজ করছেন। বিদ্যালয়টির শিক্ষকেরা বলছেন, পূর্ণকালীন প্রধান শিক্ষক না থাকলে প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো চলে না।
শিক্ষকসংকটের বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ বলেন, শিক্ষকসংকট দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিসিএসে উত্তীর্ণ, কিন্তু ক্যাডার পদ পাননি (নন-ক্যাডার) এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে।
মাউশির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখার তথ্য বলছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে আরও অবনতি হয়েছে। আগে থেকেই ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে ছিল, এবার সেই দুর্বলতা আরও বেড়েছে।
বর্তমানে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরুর পদ সহকারী শিক্ষক। সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেশির ভাগই ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে এই পদে চাকরি করে পদোন্নতি ছাড়াই অবসরে যেতেন। তবে ২০১৮ সালে ‘সিনিয়র শিক্ষক’ নামে নবম গ্রেডের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদে ২০২১ সালের জুনে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এরপর এই পদে আর পদোন্নতি হয়নি।
শিক্ষকদের অভিযোগ, প্রশাসন ও পুলিশসহ কিছু চাকরিতে পদোন্নতি পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এমনকি পর্যাপ্ত পদ না থাকলেও পদোন্নতি দিচ্ছে বর্তমান সরকার। কিন্তু শিক্ষকদের ঠিক সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হয় না।
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষক আবদুল্লাহ আল নাহিয়ান বলেন, এমনিতেই শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কম। তার মধ্যে পদোন্নতির সুযোগ সীমিত। ফলে অনেক যোগ্য তরুণ শিক্ষকতায় আসতে চান না। তাঁর দাবি, সহকারী শিক্ষকদের প্রবেশপদ নবম গ্রেড ধরে চার থেকে ছয় স্তরবিশিষ্ট পদসোপান বাস্তবায়ন করা গেলে সমস্যা অনেকটাই দূর হতো।
অনেক অভিভাবকের অভিযোগ, শিক্ষকেরা ক্লাসে ভালোভাবে পড়ানোর বদলে প্রাইভেট পড়ানোর দিকে বেশি মনোযোগ দেন। তাঁদের অনেকেই বিপুল আয় করেন। তাঁদের কাছে না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়া হয়।
স্কুলে যেনতেন পড়াশোনা
মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানা কারণে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। বছরের বড় অংশজুড়েই ছুটি থাকে। যেমন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক মোস্তাফিজুর রহমানের একটি গবেষণা প্রবন্ধ অনুযায়ী, ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪ মাসে ৪২৭ দিনের মধ্যে ২৭৯ দিনই স্কুল বন্ধ ছিল। খোলা ছিল ১৪৮ দিন।
মাধ্যমিকে একেকটি ক্লাসে (বিশেষ করে সরকারি বিদ্যালয়ে) বেশি শিক্ষার্থী থাকায় শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেককে সমান মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে পরিবারগুলো কোচিং ও গৃহশিক্ষকের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়।
২০২৪ সালের মার্চে ‘বাংলাদেশে বিদ্যালয় শিক্ষা: মহামারি উত্তর টেকসই পুনরুত্থান’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে গণসাক্ষরতা অভিযান। এতে উঠে আসে ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে পরিবারের শিক্ষার্থীপিছু শিক্ষা ব্যয় আগের বছরের (২০২২) তুলনায় প্রাথমিকে ২৫ শতাংশ এবং মাধ্যমিকে ৫১ শতাংশ বেড়েছে। এই ব্যয়ের বড় কারণ কোচিং-গৃহশিক্ষক ও নোট-গাইড।
জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো ২০২৩ সালে এক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য দিয়ে বলেছিল, বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে ব্যয়ের ৭১ শতাংশই বহন করতে হচ্ছে পরিবারগুলোকে। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের অধিক হারে ব্যয় করা উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
মাউশির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখার সাম্প্রতিক এক গবেষণার তথ্য বলছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে আরও অবনতি হয়েছে। আগে থেকেই ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে ছিল, এবার সেই দুর্বলতা আরও বেড়েছে। এমনকি বাংলায়ও শিক্ষার্থীরা আগের তুলনায় দুর্বল অবস্থায় আছে (এ বিষয়ে বিস্তারিত পড়ুন মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে)।
অনেক অভিভাবকের অভিযোগ, শিক্ষকেরা ক্লাসে ভালোভাবে পড়ানোর বদলে প্রাইভেট পড়ানোর দিকে বেশি মনোযোগ দেন। তাঁদের অনেকেই বিপুল আয় করেন। তাঁদের কাছে না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়া হয়।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী (২০১২ সালে করা) কোনো শিক্ষক তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে পড়াতে পারবেন না। তবে দিনে অন্য প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থীকে পড়ানোর সুযোগ আছে। যদিও এ নিয়ম কেউ মানেন না; বরং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে বাসা ভাড়া নিয়ে অবাধে চলে শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য।
পাঠ্যপুস্তকের বদলে নোট-গাইড এখন মাধ্যমিক শিক্ষার মূল ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একশ্রেণির শিক্ষক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে ওই সব প্রকাশনীর নোট-গাইড কিনতে বলেন শিক্ষার্থীদের।
রাজধানীর ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুলের একজন শিক্ষার্থীর বাবা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে কোচিং অথবা গৃহশিক্ষকের কাছে না পড়ালে শিক্ষার্থী ভালো ফল করতে পারে না। এ কারণে বাধ্য হয়েই তিনি সন্তানকে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ান। তিনি বলেন, সরকারি স্কুলে বেতন সামান্য। তবে গৃহশিক্ষকের খরচ অনেক।
শিক্ষকস্বল্পতা দূর করা এবং শিক্ষকদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে মাধ্যমিকে পড়াশোনার মান বাড়ানো যায়। মেধাবীদের শিক্ষকতায় আনতে আর্থিক সুবিধা ও মর্যাদা বাড়াতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে আসলে নতুন করে ভাবতে হবে।
মো. হাবিব উল্লাহ খান, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ৩ অক্টোবর অবসরে গেছেন
শিক্ষা পদ্ধতির ঘন ঘন পরিবর্তন
একে তো শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব, তার মধ্যে শিক্ষা পদ্ধতি ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষকদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। এতে শিক্ষকেরাও দক্ষতা অর্জন করতে পারেন না।
২০০৮ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়। চার বছর পর ২০১২ সালে চালু হয় নতুন শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম)। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার ২০২২ সালে নতুন আরেকটি শিক্ষাক্রম চালু করেছিল। তবে অন্তর্বর্তী সরকার নতুন এই শিক্ষাক্রম বাতিল করে দেয়। ফিরিয়ে আনা হয়েছে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম। এমন সময় তা পুনর্বহাল করা হয়, যখন নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রায় এক বছর নতুন শিক্ষাক্রমে পড়ে ফেলেছে। নবম ও দশম শ্রেণির পড়াশোনায় মিল থাকায় আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষা (কেবল এক বছরের জন্য) শুধু দশম শ্রেণির ভিত্তিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এখন আবার ২০২৭ সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রম চালুর পরিকল্পনা করছে সরকার। শিক্ষাবিদদের ভাষ্য, এত ঘন ঘন পরিবর্তনে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা আর পড়াশোনার গিনিপিগে পরিণত হচ্ছে।
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ৩ অক্টোবর অবসরে যাওয়া মো. হাবিব উল্লাহ খান তিন দশকের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতায় ছিলেন। মাঝে কিছু সময় ছিলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বেও। তাঁর মতে, শিক্ষকস্বল্পতা দূর করা এবং শিক্ষকদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে মাধ্যমিকে পড়াশোনার মান বাড়ানো যায়। মেধাবীদের শিক্ষকতায় আনতে আর্থিক সুবিধা ও মর্যাদা বাড়াতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে আসলে নতুন করে ভাবতে হবে।
মোশতাক আহমেদ
ঢাকা